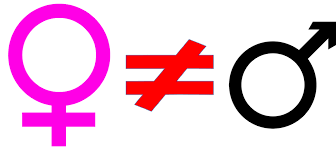পুরুষরা নারীদের চেয়ে ভিন্ন। তাদের মধ্যে একমাত্র মিল হচ্ছে তারা উভয়ই একই প্রজাতির; তারা মানুষ। কিন্তু তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা বা আচরণকে সমান বলার অর্থ হচ্ছে এক জৈবিক ও বৈজ্ঞানিক প্রতারণার ভিত্তিতে একটি সমাজ গঠন করা।
লিঙ্গদ্বয়ের ভিন্নতার কারণ তাদের মস্তিষ্কের ভিন্নতা। মস্তিষ্ক মানুষের প্রধানতম অঙ্গ, মানব আবেগের কেন্দ্র। কিন্তু নারী-পুরুষে মস্তিষ্কের গঠনের ভিন্নতা দেখা যায়; উভয়ই ভিন্নভাবে তথ্যকে বিশ্লেষণ করে। যার কারণে নারী-পুরুষের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি, চাহিদা, অগ্রাধিকার ও আচরণগত নানা পার্থক্য দেখা যায়।
লিঙ্গদ্বয়ের ভিন্নতার কারণ উদঘাটনে বিগত ১০ বছরে প্রচুর বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে। এতে আলাদাভাবে কাজ করেছেন ডাক্তার, বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা। তারা সবাই মিলে লিঙ্গদ্বয়ের ভিন্নতার একটি চিত্র দাঁড়া করিয়েছেন। চিত্রটির মূল প্রতিপাদ্যই হচ্ছে লিঙ্গদ্বয়ের অসাম্যতা।
“কেন নারীরা পুরুষদের মতো হতে পারবে না?” – অবশেষে এই প্রশ্নটির জবাব পাওয়া গেছে। বর্তমান সমাজে প্রচলিত একটি মিথ হচ্ছে নারী-পুরুষ সব দিকে সমান। পুরুষরা যা পারে, নারীরাও তা পারবে। এই সামাজিক মিথটি ভাঙ্গার সময় হয়েছে। তারা অবশ্যই সমান নয়।
কিছুদিন আগেও নারী-পুরুষের আচরণগত পার্থক্যের জন্য দায়ী করা হতো সোশ্যাল কন্ডিশনিংকে। বলা হতো যে, সমাজই নারী-পুরুষের মধ্যকার পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। পিতামাতারা সাধারণত সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হন। ফলে সমাজের প্রত্যাশাই হয় পিতামাতার প্রত্যাশা। এটি নারী-পুরুষের ভিন্নতার একটি কারণ। ছোট থেকেই ছেলেদের বলা হয় ছেলেরা কাঁদে না। আর ছেলেদের সমাজে সফলতা ও উচ্চতায় পৌঁছতে হলে পৌরুষত্ব ও আগ্রাসনমূলক মনোভাবসম্পন্ন হতে হবে। যেহেতু সমাজ ছেলেদের এসব বললেও মেয়েদের বলে না তাই পার্থক্যের পেছনে সমাজ ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরোপুরি দায়ী করা হয়। কিন্তু নারী-পুরুষের জীবগত ভিন্নতার দিকে তাকানো হয়নি। অথচ পুরুষের পুরুষ ও নারীর নারী হওয়ার মূল কারণ আমাদের এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। নারী-পুরুষের ভিন্নতার কারণ হিসেবে নতুন নতুন বায়োলজিক্যাল প্রমাণ পাচ্ছি আমরা। অবশেষে বায়োলজির যুক্তি একটি বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণযোগ্য ফ্রেমওয়ার্ক দিয়েছে যা দ্বারা প্রমাণ করতে পারব, পুরুষের পুরুষ ও নারীর নারী হওয়ার মূল কারণ কি।
পার্থক্যের সামাজিক ব্যাখ্যা অপর্যাপ্ত মনে হলে জৈবরাসায়নিক যুক্তিও আছে। সেটি হচ্ছে, আমরা হরমোনের প্রভাবে একটি নির্দিষ্ট, নির্ধারিত পন্থায় আচরণ করি। কিন্তু আমরা গ্রন্থটিতে দেখব যে এই প্রশ্নটির পূর্ণাঙ্গ উত্তর শুধু হরমোন দিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়; মূল পার্থক্য নির্ভর করে হরমোনগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়া এবং নারী বা পুরুষের মস্তিষ্ক হরমোনগুলোর প্রতি সুনির্দিষ্টভাবে কি প্রতিক্রিয়া দেখাবে তার ওপর।
এই গ্রন্থটিতে নারী-পুরুষের পার্থক্য নিয়ে পড়ার পর উভয় লিঙ্গের অনেকে ক্রোধান্বিত হতে পারে আবার কেউ কেউ আত্মতৃপ্তিও পেতে পারে। তবে উভয় প্রতিক্রিয়াই বেঠিক। নারীরা যদি রেগে যানও, তবুও তাদের বিজ্ঞানের প্রতি রাগা ঠিক হবে না। এত কষ্ট করে অর্জিত নারী-পুরুষের “সমতা”-র আন্দোলনের আগুনে পানি ঢেলে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানের ওপর রাগা অনুচিত। বরং তাদের ক্রোধান্বিত হওয়া উচিত তাদের প্রতি যারা তাদের ভুল পথে পা বাড়াতে ফুঁসলিয়েছে, তাদেরকে নারীত্বের ফিতরাত থেকে বঞ্চিত করেছে। গত ৩০ বা ৪০ বছরে অধিকাংশ নারীর ভেতর এই ভুল বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তাদেরকেও পুরুষের মতো হতে হবে। আর পুরুষ হতে যেয়ে তারা নানা অযাচিত যন্ত্রণা, হতাশা ও মনোভঙ্গের শিকার হয়েছেন। তাদের বিশ্বাস করানো হয়েছে যে, যদি তারা একবার পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শেকল ভাঙ্গতে পারে – তাহলে তারা “দ্বিতীয় শ্রেণীর” মানুষ থেকে পুরুষদের সমতুল্য পর্যায়ে উঠতে পারবে। অবশেষে নারীরা মুক্ত ও স্বাধীন হতে পারবে। বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার উচ্চ পর্যায়ে যেতে পারবে।
বিগত কয়েক দশকে নারীদের শিক্ষা, সুযোগ ও তাদের প্রতি সামাজিক মনোভাব অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। অথচ এরপরও নারীদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। কিছু ব্যতিক্রমী সফল নারীর উদাহরণ দেখিয়ে অন্য নারীদেরও ক্যারিয়ারভিত্তিক সফলতার পথে ডাকা হচ্ছে। আজকের চেয়ে ১৯৩০ সালে ব্রিটিশ কেবিনেটে নারীদের সংখ্যা বেশী ছিল। গত তিন দশকে মহিলা এমপির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি। নারীরা ক্ষমতালাভের যে স্তরে উঠতে চেয়েছিল সেখানে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা নিজেদের ব্যর্থ ভাবছে। অথচ তাদের ব্যর্থতা শুধু এক জায়গায় – তারা পুরুষদের মতো হতে ব্যর্থ হয়েছে।
কিন্তু পুরুষদেরও খুশী হওয়ার তেমন কারণ নেই। এটা সত্য যে, পুরুষরা নারীদের চেয়ে মানচিত্র ভালো বুঝতে পারে। কিন্তু মানুষের চরিত্র ভালো চেনে নারীরা। আর মানচিত্রপাঠের চেয়ে মানুষকে চেনা বেশী জরুরী।
কিছু গবেষক তাদের গবেষণার ফলাফল দেখে পুরোপুরি হতাশ হয়েছেন। কারো কারো গবেষণার ফল চেপে যাওয়া হয়েছে, নয়তো গবেষণার সামাজিক প্রভাবের কথা বিবেচনা করে গবেষণা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে সত্যকে মেনে নেওয়াই সর্বোত্তম কাজ। তাই সত্যের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। সত্যের বাইরে গিয়ে সামাজিক প্রভাবকে গুরত্ব দেওয়া হবে মারাত্মক ভুল।
নারী-পুরুষের মধ্যকার পরিপূরক পার্থক্যগুলোকে স্বাগত জানানো উচিত। নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করে পুরুষ হওয়ার পেছনে না ছুটে নারীদের উচিত নারীত্বের উপহারকে বরণ করে নেওয়া। নারীরা তাদের প্রবল কল্পনাশক্তি দ্বারা কল্পনার তুলির এক আঁচড়েই ঘরোয়া বা পেশাকেন্দ্রিক নানা সমস্যার সমাধান করতে পারে।
নারী-পুরুষের মধ্যকার পার্থক্য মেনে নেওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে, এমনটা করতে পারাই আমাদের সুখী করবে। উদাহরণস্বরূপ, পুরুষ ও নারীর মস্তিষ্কে যৌনতার উৎস, উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য ভিন্ন অর্থ বহন করে। এটা অনুধাবন করতে পারলে আমরা ভালো স্বামী বা স্ত্রী হতে পারব। বাবা-মায়ের ভূমিকা যে পুরুষ-নারীর মধ্যে বিনিময়যোগ্য নয়, এটা বুঝতে পারলে আমরা বাবা-মা হিসেবে সন্তানের প্রতি দায়িত্ব আরো ভালোভাবে পালন করতে পারব।
নারী-পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আচরণগত পার্থক্য হল পুরুষদের স্বাভাবিক, সহজাত আগ্রাসন। ঐতিহাসিকভাবেই সর্বদা পুরুষরা সমাজে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে। পুরুষরা যৌনযুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য আগ্রাসী হতে শেখেনি। আমরা আমাদের ছেলেদের আগ্রাসী হতে শেখাই না। বরং এটা শেখানোর চেষ্টা করাই বৃথা। এমনকি যেসব গবেষকরা নারী-পুরুষের পার্থক্য মানার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অনড় তারাও আগ্রাসনকে পুরুষদের যৌনবৈশিষ্ট্য হিসেবে মেনে নেন। একে সোশ্যাল কন্ডিশনিং দ্বারা ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ নেই।
লেখক এইচ. এইচ. মনরো একটি শিক্ষামূলক অনুগল্প লিখেছেন যেখানে একটি লিবারেল পরিবারের গল্প বলা হয়। পিতামাতা তাদের সন্তানের পৌরুষবৃত্তিক আগ্রাসনকে দমিয়ে রাখার জন্য তাকে খেলনা সৈন্যের ফিগার কিনে না দিয়ে শিক্ষক ও সাধারণ নাগরিকের খেলনা ফিগার কিনে দেন। তাদের মনে হচ্ছিল সব ঠিকঠাকই যাচ্ছে। কিন্তু একদিন তারা ছেলের খেলার ঘরে ঢুকে দেখেন ছেলেটা খেলনা শিক্ষক বনাম খেলনা ক্ষমতাসীন আমলার যুদ্ধ বাধিয়েছে। ছেলেটাকে ভাগ্যবানই বলতে হবে। কারণ তার পিতামাতা বুঝতে পেরেছিলেন তারা অনর্থক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, প্রকৃতির চাহিদার বিপরীত কিছু বানাতে চেয়েছেন ছেলেকে; যা কখনোই সম্ভব নয়।
আমরা জাতি হিসেবে খুব অহংকারী। আমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ও অতি বুদ্ধিমান মনে করি। নিজেদের নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা ভাবি। অথচ আমাদের জৈবিক দিক দিয়ে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটাকে পুরোপুরি এড়িয়ে যাই। আমাদের সাথে কি ঘটবে, আমরা কিভাবে চলব তা অনেকাংশেই নির্ভর করে আমাদের গঠনের ওপর।
আমরা নারী-পুরুষের পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারলে উভয়ই আরো সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারবে। একে-অপরকে বুঝতে পারবে, ভালোবাসতে পারবে। পৃথিবীটাকে আরো সুন্দর করতে পারবে। আমরা আমাদের ভিন্ন যৌন পরিচয়ের ভিত্তিতে জীবন ও সমাজ গড়ে তুলতে পারব। সময় হয়েছে নারী-পুরুষ পুরোপুরি সমান – এই বাতিল চিন্তাকে পরিত্যাগ করার। তারা কখনো সমান ছিল না, শত প্রচেষ্টা চালালেও কোনোদিন হবে না। বরং এর ফলে উভয় লিঙ্গের মধ্যকার সম্পর্কে আরো দূরত্ব বাড়বে।
পুরুষ যেসব ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও দুর্বল নারী সেসব ক্ষেত্রে যথাক্রমে দুর্বল ও শক্তিশালী। এভাবে তারা একে-অপরের পরিপূরক। এটা অনুধাবন করতে পারলে উভয় লিঙ্গের মধ্যকার বন্ধন শক্তিশালী হবে এবং লিঙ্গদ্বয়ের মধ্যে সুখী সম্পর্কের সৃষ্টি হবে।
একটা পুরোনো কৌতুক আছে। একটা খুব পাতলা বইয়ের নাম “পুরুষরা নারীদের যা যা বোঝে”। কয়েক পৃষ্ঠার বইটির পৃষ্ঠাগুলো একদম ফাঁকা।